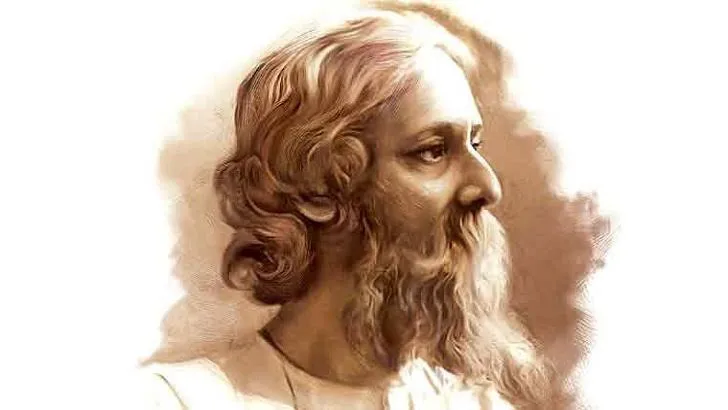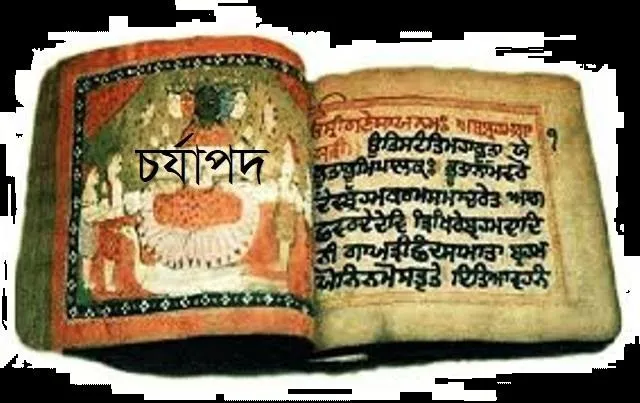কখনো কখনো মহৎ ব্যক্তিরা একই ভাবে চিন্তা করেন। তাদের এই চিন্তার সাযুজ্য আমাদেরকে দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়.. আমরা সন্দেহ পোষণ করি প্লেজিয়ারিজম নিয়ে।
এটা স্বাভাবিক। শত শত বৎসরের এই পৃথিবীতে কয়েকজন গুণী মানুষের চিন্তার মিল হতেই পারে। এজন্য অনেক সময় দেখা যায়.. একজনের লেখার সাথে অন্যজনের লেখা মিলে যায়.. একজনের গানের সুরের সাথে অন্যজনের গানের সুর মিলিয়ে যায়.. এই কাকতালীয় সাযুজ্যের কারণে এমনকি অনেক মহৎ সাহিত্যিককে ভাব চুরির জন্য দায়ী পর্যন্ত করা হয়েছে!
আজ বাংলা সাহিত্যের এরকম একটি অসাধারণভাবে সাযুজ্য নিয়ে আলোচনা করব.. যার সাথে জড়িত আছে বাংলা সাহিত্যের দীপ্তমান সূর্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার পূর্বে চর্যাপদ নিয়ে কিছু কথা বলি-
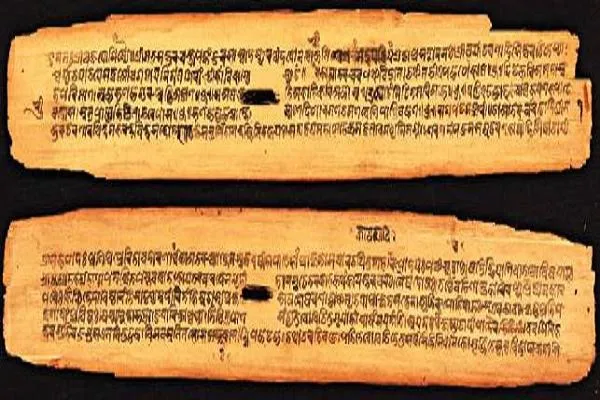
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। আমি যখন প্রথম চর্যাপদ পড়তে শুরু করি.. এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে.. বেশ কিছুদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না.. হাজার বছর আগে পাহাড়ের চূড়ায় বসে কতিপয় সমাজত্যাগী সন্ন্যাসী কিভাবে এই অসাধারণ পংক্তিগুলো রচনা করেছিল!
চর্যাপদের পদগুলো ছিল এক ধরনের গান.. যা সুরারোপ করে গাওয়া হতো.. এজন্য সেগুলোকে বলা হতো চর্যাগীতিকোষবৃত্তি। কিন্তু কখনো কখনো গানের কথা কবিতার গভীরতাকেও ছাড়িয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা লালন সংগীত কিংবা আধুনিককালে বব ডিলানের কথা বলতে পারি। কিংবা পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত গায়ক কবীর সুমনের কথাও উল্লেখ করা যায়।
চর্যাগীতি ছিল তারও চেয়ে গভীর। এর চেয়ে বড় কথা, প্রাচীন সাহিত্যগুলোর মধ্যে যদি তুলনামূলক পর্যালোচনা করি- ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং অন্যান্য ভাষার পুরাতন নিদর্শনগুলোর তুলনায় বাংলা ভাষার পুরাতন নিদর্শন চর্যাপদ কোন অংশে পিছিয়ে নেই! বরং অন্যান্য ভাষার প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে গল্প বলার প্রবণতার আধিক্য এবং গভীর জীবনবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে ক্ষেত্রে চর্যাপদ ব্যাতিক্রম। চর্যাপদ কোন উপাখ্যান নয়.. ধর্মীয় কিছু অনুষঙ্গের আড়ালে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন চর্যাপদের কবিরা..
ছাত্রাবস্থায় আমি চর্যাপদের ভাবানুবাদ করেছিলাম ছন্দে ছন্দে। এটা করতে গিয়ে দুইটি লাইনে এসে আমি হঠাৎ একটা ধাক্কা খাই। পংক্তি দুটি হল:
সোনে ভরিলি করুণা নাবি
রুপা থুই নাহিক ঠাবি।
আমরা জানি, চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় সান্ধ্য ভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারির ভাষা। এটা শুধুমাত্র শব্দগুলোর দুর্বোধ্যতার কারণে নয়, বরং শব্দের পাশাপাশি অর্থ ও ভাবের আলো-আঁধারীর কারণেও এটাকে সান্ধ্য ভাষা বলা হয়।
উদাহরণ হিসেবে যে দুটি পংক্তি উল্লেখ করেছি, সেগুলোর কথাই বলা যায়। বাক্যদুটির একই সাথে দুই ধরনের অর্থ করা যায়। কারণ চর্যাপদের কবিগণ ইচ্ছা করেই এমনভাবে শব্দ ব্যবহার করেছেন যেন ভিন্নভাবে চিন্তা করলে ভিন্ন অর্থ পাঠকের মানসপটে ধরা পড়ে।
'সোনে' শব্দটার একটি অর্থ স্বর্ণ, অন্য অর্থ শূন্য
'রুপা' শব্দটির একটা অর্থ রৌপ্য, অন্য অর্থ রূপ
আমরা যদি প্রথম অর্থগুলো নেই, তাহলে পংক্তি দুটোর সরল বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায়: স্বর্ণ দিয়ে নৌকা ভর্তি করে ফেলেছ, রুপা রাখার জায়গা নেই।
আর যদি দ্বিতীয় অর্থগুলো নেই, তাহলে সরল বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায়: শূন্য দিয়ে নৌকা ভর্তি করে ফেলেছ, রূপ অর্থাৎ বস্তু রাখার জায়গা নেই। কি অসাধারণ চিন্তা ধারা!
বেশিরভাগ কবিরা অনুবাদ করতে গিয়ে প্রথম অর্থ দুটোই নিয়েছেন। যদিও দ্বিতীয় অর্থটা আমার বেশি ভালো লাগে.. শূন্য দিয়ে কোন কিছু পূর্ণ করা.. অর্থাৎ নৌকা জুড়ে শুধু শূন্যতা এবং এই শূন্যতার ভেতরে কোন বস্তুবাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা.. এটা অসাধারণ একটা দার্শনিক চেতনা.. এই ধরনের গভীর জীবনবোধ ও দর্শন এই সময়ের সাহিত্যেও দুর্লভ।
কিন্তু বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকাররা সহজ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার জন্য প্রথম ব্যাখ্যাটিই নিয়েছেন। এখানে এসেই আমি ধাক্কাটা খাই। স্বর্ণ দিয়ে নৌকা ভর্তি করে ফেলেছ, রুপা রাখার জায়গা নেই। এই অনুবাদ করতে গিয়ে আমার মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অসাধারণ কবিতা সোনার তরীর কয়েকটি লাইন:
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই
ছোটো সে তরী
আমার সোনার ধানে
গিয়েছে ভরি।
কি অসাধারণ মিল! মনে হচ্ছে যেন কবিগুরু চর্যাপদ থেকেই বাক্য দুটি প্লেজিয়ারিজম করেছেন। অথচ কবিগুরু 'সোনার তরী' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৮৯৪ সালে.. আর চর্যাপদ প্রথম আবিষ্কার হয় আরও ১৩ বছর পরে।
পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী১৯০৭ সালে নেপাল ভ্রমণকালে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক একটি পুঁথি নেপাল রাজদরবারের অভিলিপিশালা থেকে আবিষ্কার করেন। তারপর তিনি তার সংগৃহীত চারটি গ্রন্থ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব পুঁথি একত্রে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোঁহা’ শিরোনামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। এটাই চর্যাপদের আবিষ্কার ও প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
তার মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন 'সোনার তরী' কবিতাটি লেখেন.. তখন চর্যাপদের অস্তিত্ব নেপালের রাজদরবারে গুপ্ত ছিল.. যেটা ভারতবর্ষের কেউ জানতো না.. রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তো জানা সম্ভবই ছিল না। এটা কেবলমাত্র একটা ভাবের পুনর্জন্ম.. অথবা কাকতালীয় সাযুজ্য!
রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, সংগীতে এরকম আরো অনেক ভাবের পুনর্জন্ম পাওয়া যায়। অনেক আনকোরা সমালোচক কবিকে সেগুলোর জন্য সরাসরি প্লেজিয়ারিজমের দায়ে অভিযুক্ত পর্যন্ত করেছেন। অন্য কোন লেখায় তাদের সেই ভুল তথ্য গুলো খণ্ডন করব।
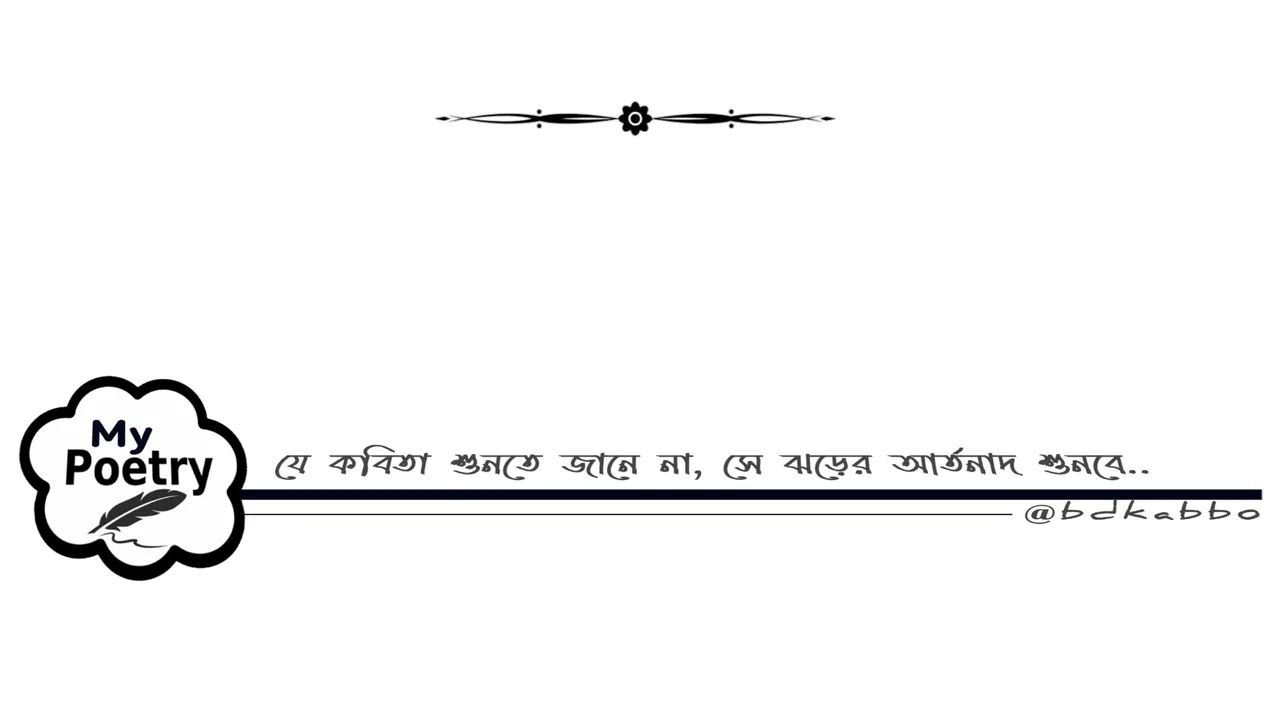
আমার পরিচিত:
আমি কাব্য.. কবিতা এবং সাহিত্য ভালোবাসি.. নিজেও কিছু লেখার চেষ্টা করি.. হয়, আবার হয় না..